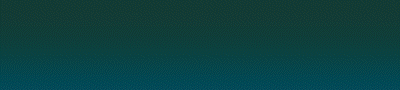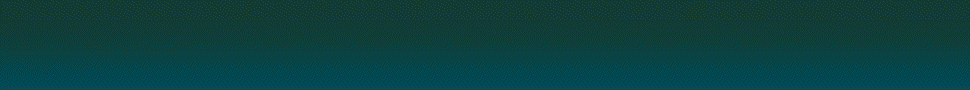ইতিহাস
হাটখোলা-বটতলার বৈশাখি মেলা

বাঙালির জীবনে পহেলা বৈশাখ যেন এক নবজাগরণের দিন। পুরনো জীর্ণতা আর কষ্ট ভুলে গিয়ে নতুন সূর্যের আলোয় ভর করে সামনে এগিয়ে চলার অঙ্গীকারের নামই পহেলা বৈশাখ। আর এই নববর্ষ উদযাপনের সবচেয়ে প্রাণবন্ত আয়োজনটি হলো বৈশাখী মেলা—যা যুগ যুগ ধরে আমাদের গ্রামবাংলার লোকজ সংস্কৃতির এক অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়েছে।
এক সময় বৈশাখী মেলা ছিল কেবল গ্রামের আয়োজন। মেলা বসত গ্রামের মাঠে, বটতলায়, নদীর ধারে কিংবা কয়েকটি গ্রামের সীমান্তবর্তী কোনো উন্মুক্ত জায়গায়। সেই মেলায় নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবাই ভিড় করত। মেলার দিনটি ছিল সবার জন্য আনন্দের, কেনাকাটার, আড্ডা ও বিনোদনের। দূর-দূরান্তের মানুষজন, নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ, মেলার টানে এসে মিলিত হতেন এক প্রাণের বন্ধনে।
মেলায় পাওয়া যেত নানা ধরনের পণ্য—কুটির ও হস্তশিল্প, কৃষিপণ্য, কাঁচের চুড়ি, তাঁতের শাড়ি, বাঁশের তৈজসপত্র, মাটির খেলনা, পুতুল, হাতপাখা, অলংকার, চিড়া-মুড়ি-খই, বাতাসা, সন্দেশ, মিষ্টি—আরো কত কিছু! বাচ্চাদের জন্য থাকত নাগরদোলা, বায়োস্কোপ, পুতুলনাচ। আর বিনোদনের দিক দিয়ে থাকত লাঠিখেলা, জারি-সারি-ভাটিয়ালি গান, কবিগান, কুস্তি খেলা, কখনোবা ষাঁড়ের লড়াইও। এই মেলাই ছিল একদিকে প্রাণের উৎসব, অন্যদিকে জীবিকার অবলম্বন।
বৈশাখী মেলার ঐতিহাসিক সূত্র খুঁজতে গিয়ে জানা যায়, বিশ্বের প্রাচীনতম মেলার একটির আয়োজন হয়েছিল হিমালয়ের কোলে, হরিদ্বারে প্রায় দুই হাজার বছর আগে। ভারতবর্ষে শিল্পপণ্যকেন্দ্রিক মেলার সূত্রপাত হয় ১৭৯৭ সালে। বাংলা অঞ্চলে বৈশাখী মেলার প্রচলন ঘটে বাংলা সনের সূচনার পরে, যখন বাদশাহ আকবর নতুন রাজস্ব বর্ষ হিসেবে পহেলা বৈশাখ চালু করেন। তারপর থেকেই কৃষক, মেহনতি মানুষ, ব্যবসায়ী সবাই নববর্ষকে ঘিরে উৎসবে মেতে উঠতে শুরু করেন।
ধারণা করা হয়, ১৮৬৪ সালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে প্রথমবারের মতো পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান করা হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মেলার মাহাত্ম্য বোঝাতে বলেছিলেন—"মেলাই আমাদের পল্লীর প্রধান উপায় বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্ত চলাচল অনুভব করিবার জন্যে।" সত্যিই তো, এই মেলার মধ্য দিয়ে গ্রামের মানুষ বৃহত্তর সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়, এবং নিজের সংস্কৃতিকেও অন্যের মাঝে বিলিয়ে দেয়। এটি শুধু বেচাকেনার জায়গা নয়, বরং এটি হয়ে ওঠে এক প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন।
এক সময় বৈশাখী মেলা ছিল গ্রামভিত্তিক সংস্কৃতির অংশ। তবে কালের পরিবর্তনে আজ মেলাটি শহরে এসে স্থায়ী আসন গেড়েছে। শহরজীবনের ব্যস্ততার মাঝেও বৈশাখী মেলা হয়ে উঠেছে নাগরিকদের প্রাণের আয়োজন। ১৯৭৭ সালে বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গণে প্রথমবারের মতো শহরে বৈশাখী মেলার আয়োজন হয় সাহিত্যপত্র ‘সমকাল’-এর সহযোগিতায়। বিশিষ্ট শিল্পী কামরুল হাসান ও ফোকলোরবিদ শামসুজ্জামান খান এ আয়োজনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। মূল উদ্দেশ্য ছিল বাঙালির ঐতিহ্যকে শহরের মানুষের সামনে উপস্থাপন করা—যা নিঃসন্দেহে সফল হয়েছিল।
আজকের দিনে ঢাকার রমনা পার্ক, বাংলা একাডেমি, চারুকলা ইনস্টিটিউট, জাতীয় জাদুঘর, শিশু একাডেমি, ধানমণ্ডি রবীন্দ্রসরোবরসহ নানা স্থানে বসে বৈশাখী মেলা। শহরের মেলায়ও থাকে দেশি পোশাক, গহনা, হস্তশিল্প, চিত্রকর্ম, খাবারদাবার, লোকসংগীত, নাটক, পুতুলনাচসহ নানামুখী আয়োজন। তবে গ্রামীণ বৈশাখী মেলার যে সারল্য, প্রাণচাঞ্চল্য, এবং শিকড়ের টান—তা হয়তো শহরে পুরোপুরি ধরা পড়ে না।
আজকের দিনে কিছুটা আশঙ্কার কথা হলো, গ্রামে আগের মতো আর বৈশাখী মেলার আয়োজন হয় না। আধুনিকতার ছোঁয়ায় আর শহরমুখী সংস্কৃতির চাপে গ্রামবাংলার লোকায়ত শিল্প ও সংস্কৃতি অনেকটাই হারিয়ে যাচ্ছে। সেইসব পেশাজীবীরা—যারা বাঁশের তৈরি জিনিস, মাটির পুতুল বা হাতের কাজের শাড়ি তৈরি করতেন, তারাও আজ অন্য জীবিকার খোঁজে বাধ্য হচ্ছেন পথ পাল্টাতে। ফলে লোকজ ঐতিহ্য যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তেমনি দেশের শিকড়ও ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ছে।
তবুও এখনো কিছু জায়গায় গ্রামীণ বৈশাখী মেলার ধারা অব্যাহত রয়েছে। যেমন ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, বরিশাল, খুলনা, ধামরাই—এসব জায়গায় আজও পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে গ্রামীণ মেলা বসে। লোকজ শিল্পীরা এখনো প্রাণপণে চেষ্টা করছেন নিজেদের শিল্প বাঁচিয়ে রাখতে।
বৈশাখী মেলা কেবল একটি ঐতিহ্যবাহী উৎসব নয়, এটি গ্রামীণ অর্থনীতির একটি বড় চালিকাশক্তিও। এ মেলার সঙ্গে সরাসরি জড়িত তাঁতি, কামার, কুমোর, কুটিরশিল্পী, খেলনার কারিগর, বাদ্যযন্ত্র নির্মাতা, মিষ্টি ব্যবসায়ী, বাঁশ-কাঠের কারিগর প্রভৃতি। বৈশাখী মেলা তাদের জন্য শুধু পণ্য বিক্রির জায়গা নয়—এটি তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের কষ্টের ঘামে তৈরি পণ্য বিক্রি হয় এই মেলায়, আর সেখান থেকেই তারা নতুন দিনের আশায় বুক বাঁধেন।
অতএব, বৈশাখী মেলা শুধু একটি লোকজ উৎসব নয়; এটি আমাদের শিকড়ের সন্ধান, আমাদের সংস্কৃতির আত্মপরিচয়। এ মেলার মধ্যে আমরা পাই আমাদের মাটি ও মানুষের ঘ্রাণ। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যদি আমরা এই মেলাকে রক্ষা করতে পারি, শহরের সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গ্রামীণ ঐতিহ্যকেও তুলে ধরতে পারি—তাহলে আমাদের এই অসাধারণ লোকায়ত উৎসব কখনো হারাবে না।