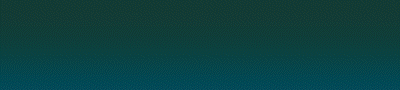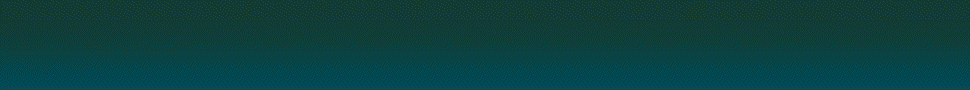বাংলাদেশ ও বেইজিংয়ের দ্বিপাক্ষিক ভারসাম্য

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের চীন সফরটি এসেছে বাংলাদেশের পরিবর্তিত ভূ-রাজনৈতিক ও অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে। সফরটি বাংলাদেশ-চীন সম্পর্কের গুরুত্বকে তুলে ধরলেও এটি অবশ্যই বাংলাদেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করতে হবে।
আগস্ট বিপ্লব দেশের গতিপথকে নাটকীয়ভাবে বদলে দিয়েছে, যা কূটনৈতিক সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে নতুন প্রত্যাশা তৈরি করেছে। তবে এই সফরকে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পূর্ণ নতুন সংযোগ হিসেবে দেখা হবে বিভ্রান্তিকর। কারণ, এই সফরে সই করা চুক্তিগুলোর বেশির ভাগই গত সরকারের শাসনামলে নির্ধারিত অগ্রাধিকারগুলোর ধারাবাহিকতা বহন করে, যা চীনের নীতিগত স্থায়িত্বকে তুলে ধরে।
বাংলাদেশের প্রতি চীনের কৌশলগত ধারাবাহিকতা সুস্পষ্ট। বেইজিং ঐতিহাসিকভাবেই ঢাকার সঙ্গে রাজনৈতিক পরিবর্তন নির্বিশেষে সম্পর্ক বজায় রেখেছে। ২০১৬ সালে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের ঢাকা সফরের সময় খালেদা জিয়ার সঙ্গে তার বৈঠকই এই নীতির প্রমাণ।
ড. ইউনূসের সাম্প্রতিক সফরের পর যৌথ বিবৃতিও চীনের অর্থনৈতিক সহযোগিতা, অবকাঠামো উন্নয়ন ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে, যা নির্দিষ্ট কোনো বাংলাদেশি সরকারের প্রতি নয়, বরং বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রতি চীনের অঙ্গীকারকে প্রকাশ করে।
এই সফরের অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো— আগস্ট-পরবর্তী বাংলাদেশের পটভূমিতে বাংলাদেশে এরই মধ্যে বিদ্যমান ভারতবিরোধী মনোভাব প্রত্যক্ষ, স্পষ্ট ও এমনকি বাড়তেও শুরু করেছে। আগস্ট বিপ্লবের পর বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রূপান্তরের বাইরে ইতিবাচক কূটনৈতিক ফলাফল দেখানোর প্রয়োজনীয়তা ইউনূসের সফরকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। আর এই আবেগতাড়িত মনোভাব অন্তত কূটনৈতিক বিবেচনায় অবাস্তব আকাঙ্ক্ষারও জন্ম দেয়। তবে কৌশলগত বিশ্লেষণে বোঝা যায়, চীনের সম্পৃক্ততা প্রতিক্রিয়াশীল নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ।
অর্থনৈতিক সহযোগিতা, অবকাঠামো উন্নয়ন ও বাণিজ্য সম্প্রসারণ সংক্রান্ত চুক্তিগুলো চীনের দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্যগুলোর ধারাবাহিকতা বহন করে। মোংলা বন্দর প্রকল্প ও চীন-বাংলাদেশ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) নিয়ে চলমান আলোচনা চীনের দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। এফটিএ আলোচনাও এই সফরের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। তবে এটি এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। যদিও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শেষ হয়েছে, কার্যকর আলোচনায় এখনো অগ্রগতি সীমিত। বরং চুক্তির আলোচনা বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার করার প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।
উল্লেখযোগ্য, যৌথ বিবৃতিতে বাংলাদেশ আবারও ‘এক-চীন’ নীতির প্রতি প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে, যা ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশের অবস্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও বর্তমান বহুপাক্ষিক বিশ্বে এর কূটনৈতিক গুরুত্ব বেড়েছে। গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (জিডিআই) নিয়ে বাংলাদেশের আগ্রহও উল্লেখ্যযোগ্য বার্তা বহন করে। বৈশ্বিক দক্ষিণের পুনর্গঠনের প্রক্রিয়ায় এই উদ্যোগ চীনের সম্ভাব্য ভূমিকা ও বাংলাদেশের জন্য সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে।
বহুপাক্ষিকতার প্রতি উভয় দেশের প্রতিশ্রুতি বিশ্বব্যবস্থার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গ্লোবাল দক্ষিণকে সংহত করার লক্ষ্যকে আরও সুসংহত করেছে। বতমান বৈশ্বিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ বার্তাগুলো গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমা বিশ্ব তথা যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন বিশ্বব্যবস্থার প্রহসন, অনিয়ম ও পশ্চিমা স্বার্থান্বেষী অভিলাষ যেখানে ক্রমশ স্পষ্ট, সেখানে একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থার সূচনার জন্য ছোট ছোট পদক্ষেপ নিয়ে বিবেচনা করাটা জরুরি।
প্রধান উপদেষ্টার এই সফরের প্রভাব কেবল অর্থনৈতিক সহযোগিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। স্বাস্থ্য খাতে সহযোগিতার প্রসার কৌশলগত ও উন্নয়নমূলক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ। স্বাস্থ্য অবকাঠামো উন্নয়নের এই প্রচেষ্টা কেবল বাংলাদেশের জনগণের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং এটি ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক টানাপোড়েনের ক্ষেত্রেও জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
প্রধান উপদেষ্টার সফরটি যদিও বাংলাদেশের কূটনৈতিক অবস্থানকে শক্তিশালী করার সুযোগ তৈরি করেছে, তবে এটি আঞ্চলিক নিরাপত্তা, বিশেষ করে পানিবণ্টন ও রোহিঙ্গা সংকটের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর সামনে নতুন প্রশ্নও তুলেছে। যৌথ বিবৃতিতে চীনের সম্পৃক্ততা পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে, যা দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে চীনের অপরিহার্য ভূমিকার ইঙ্গিত দেয়। তবে এ বিষয়ে বাস্তব অগ্রগতি এখনো অনিশ্চিত।
যমুনা নদীর পানিবণ্টন সংক্রান্ত ‘হাইড্রোলজিক্যাল ইনফরমেশন শেয়ারিং’ চুক্তি একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হলেও বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি জল-নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আরও সুসংগঠিত সহযোগিতা প্রয়োজন।
তিস্তা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্পে চীনের সম্ভাব্য অংশগ্রহণ বাংলাদেশের বিকল্প অংশীদারির ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করে। তবে এই প্রেক্ষিতে ভারতের সংশ্লিষ্টতা থাকায় এটি কূটনৈতিকভাবে সংবেদনশীল একটি বিষয়, যা সতর্কতার সঙ্গে পরিচালনা করা জরুরি। ঢাকার এই নতুন পদক্ষেপ ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন আরও বাড়াতে পারে।
চীনের ব্রহ্মপুত্র বাঁধ প্রকল্পের প্রভাব নিয়ে এখনো কোনো কার্যকর চুক্তি হয়নি, যা বাংলাদেশের জলবায়ু নিরাপত্তার জন্য উদ্বেগজনক। এ ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন ও সামুদ্রিক সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য অপরিহার্য।
বাংলাদেশ চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই) সফরের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। সফরে কিছু নতুন প্রকল্প ঘোষণা করা হলেও মূল ফোকাস ছিল বিদ্যমান প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা। তবে কিছু বিআরআই প্রকল্পের কৌশলগত মূল্য নিয়ে সমালোচনা অব্যাহত রয়েছে এবং এই সফর সে বিতর্কের মোড় কতটুকু পরিবতন করতে পেরেছে তা ক্রমশ প্রকাশ্য।
সর্বশেষে, ড. ইউনূসের সফরটি বাংলাদেশ-চীন সম্পর্কের ধারাবাহিকতাকেই নিশ্চিত করেছে। এটি বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানকে সংহত করতে ভূমিকা রাখলেও তাৎক্ষণিক বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে এ সফরের তেমন কোনো বড় পরিবর্তন আসার কথাও ছিল না। সফরটি কোনো নতুন চুক্তি আলোচনার উদ্দেশ্যে ছিল না, বরং এটি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার অংশই ছিল।
প্রধান উপদেষ্টার এই সফরকে ব্যর্থ বলে অভিহিত করা হলে তা কূটনৈতিক বাস্তবতাকে বুঝতে ব্যর্থ হওয়ার শামিল হবে। বিশেষ করে যখন এটি ছিল ৯ মাসের ব্যবধানে সরকারপ্রধান পর্যায়ের দ্বিতীয় সফর, তখন বড় কোনো অগ্রগতি আশা করাটা ছিল অযৌক্তিক। সফরটি আসলে ছিল কৌশলগত স্থিতিশীলতার প্রতিচিত্র, যা বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানকে পুনর্ব্যক্ত করেছে এবং চীনের দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতার বার্তাও বহন করেছে।
লেখক: রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশ্লেষক